204. পার্বত্য শান্তিচুক্তি
ভূমিকা: যেকোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয় যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্বাধীনভাবে কাজ করে। স্বাধীনতার পর দেশের অগ্রগতির পথে বাধা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা ঘটে। প্রায় দুই যুগ ধরে আত্মঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত শান্তিবাহিনীর সাথে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৪০
মিনিটে ‘শান্তিচুক্তি’ নামক এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।
মিনিটে ‘শান্তিচুক্তি’ নামক এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।
চুক্তি সম্পাদন: তৎকালীণ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু করে। তারা এ সমস্যা সমাধানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত এর সাফল্য হিসেবে ঐতিহাসিক এক আনন্দঘন মুহূর্তে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ শান্তি চুক্তিতে সরকার পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও পার্বত্য জনসংহতি সমিতির পক্ষে সংগঠনের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা। এ চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।
ইতিকথা: ১৯০০ সালের পহেলা মে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে ‘শাসন বহির্ভূত এলাকা’ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর ১৯২০ সালে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি’ গঠিত হয় যারা ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানি শাসন কায়েমের বিপক্ষে ছিল। অতঃপর ১৯৫৭ সালে র্যাডক্লিফ মিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৬০ সালে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হলে বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় পরিবার তাদের ফসলি জমি ও বাস্তুভিটা হারায়। এ সময় বিপুল সংখ্যক পাহাড়ী জনগোষ্ঠী দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার উপজাতীয়দের মধ্য থেকে রাজাকার, ওসি, এ.এফ, হওয়ার জন্য লোক রিক্রুট করে এবং চাকমা রাজা ত্রিদির রায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। যার ফলে পাহাড়ীরা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের রোষানলে পড়ে। এরপর ১৯৭২ সালে উপজাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার ফলে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সন্তু লারমার নেতৃত্বে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’ নামে পাহাড়ি জনগণের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাদের বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন। এর ফলে পাহাড়ীরা নিয়মতান্ত্রিক স্বাভাবিক রাজনীতির প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি তাদের আর্মড ক্যাডার ফোর্স ‘শান্তিবাহিনী’ গঠন করে। পরবর্তীতে এ বাহিনী প্রথমে স্বাধিকার, পরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জুমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে শুরু করলে পাহাড়ী-বাঙালি মিলিয়ে প্রায় ২০ সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়।
শান্তি বাহিনীর গেরিলা কার্যক্রম ও সরকারি পদক্ষেপ: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান-এর হত্যাকান্ডের ফলে জনসংহতি সমিতির সংকটময় অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সন্তু লারমা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। ১৯৭৫-১৯৭৭ সালের মধ্যে শান্তিবাহিনী সামরিক দিক দিয়ে অধিকতর সংগঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে সংগঠিত শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সরকার সামরিক পথেই পাহাড়ীদের এ অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে দরিদ্র ভূমিহীন প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করেন। এ ঘটনা পাহাড়ীদের আতঙ্কিত করে তোলে। ৬০, ৭০ ও ৮০-এর দশকে মানবেন্দ্র লারমা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মু জাতীয়তাবাদের বিকাশে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন বিহারী খাসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা প্রমুখ।
অতীত শান্তি আলোচনা: পার্বত্য সশস্ত্র সংঘাত অবসানের জন্য প্রথম জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা করা হয় ১৯৮৫ সালে, জেনারেল এইচএম এরশাদের শাসনামলে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এই শান্তি আলোচনা চলে। এই সময় ১৯৮৯ সালের ২ জুলাই তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের অধীনে স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে। নিয়ম করা হয় প্রতি জেলায় ৩০ জন সদস্য রাখা হবে। যার এক-তৃতীয়াংশ বাঙালি এবং দুই তৃতীয়াংশ বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠী। কিন্তু সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন শান্তিবাহিনী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে এই পরিষদের হাতে যে ২২ ধরণের ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শান্তি বাহিনীর সঙ্গে ১৩ দফা বৈঠক হয়। তারপর ১৯৯৬ সালের ২২ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় বসার পর শান্তিবাহিনীর সাথে আবার নতুন করে আলোচনার উদ্যোগ নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রধান হিসেবে মনোনীত হন তৎকালীন চীফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ।
পাঁচ দফা পেশ: কমিটির প্রধান শান্তি আলোচনার পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ১ আগস্ট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র বিরতি শুরু করেন। তখন জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে আলোচনা করে ৫ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো নিম্নরূপ-
১। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বাধীন পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান, যার নাম হবে জুম্মুল্যান্ড।
২। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের জাতিগত সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।
৩। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের প্রত্যাহার। পার্বত্য ভূমির ওপর পাহাড়ি স্বত্ত্বের স্বীকৃতি।
৪। বিডিআর ক্যাম্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস তুলে নেয়া।
৫। ১৯৬০ সালের পর থেকে যে সব পাহাড়ি চট্টগ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আইনি অভিযোগ প্রত্যাহার এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিষয়বস্তু: পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রধান বিষয়বস্তু হলো দ্বিস্তর বিশিষ্ট পরিষদ। যার প্রথমটি আঞ্চলিক পরিষদ, পৃথক তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। স্থানীয় সরকার পরিষদের পরিবর্তে জেলা পরিষদ গঠিত হবে। আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয় করবে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এ তিনটি জেলা পরিষদ। যা দুই যুগের বেশি সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।
পার্বত্য শান্তি চুক্তির দিকসমূহ: মোট ২৬টি বৈঠক শেষে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অশান্ত পার্বত্য অঞ্চলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- স্বাক্ষরের পর থেকেই চুক্তি বলবৎ হবে।
- বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলী কদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারি, আধা সরকারি, পরিষদীয় ও সায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সকল স্তরে নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হবেন।
- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোকন করা হবে।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমান এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।
- পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। দুই-তৃতীয়াংশ উপজাতীয় হবে।
- পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর হবে।
- পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া কোনো জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে।
- কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।
- মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হবে।
- তিন জেলা সমন্বয়ে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এর মেয়াদ হবে ৫ বছর।
- সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে চাইলে সরকার পরিষদের সাথে আলাপ করবে।
উপরিউক্ত নীতিমালার ভিত্তিতেই সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
পার্বত্য শান্তিচুক্তির প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ (ফলাফল): এই শান্তিচুক্তির ফলে পাহাড়ি এলাকায় বিদ্যমান যে হানাহানি তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে সন্তু লারমা দলের ৭৩৯ অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে। অন্যান্য বিরোধীরাও পরবর্তীতে অস্ত্র জমা দেয়। প্রায় ৬৪০০০ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। এই শান্তিচুক্তির ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’ পত্রিকা মন্তব্য করে, ‘এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের একটি বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে।’ ইউনেস্কো বাংলাদেশের এই পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে স্বীকৃতিস্বরূপ শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে। পক্ষান্তরে এ চুক্তি ‘স্মরণকালের শান্তি চুক্তি’ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।
উপসংহার: পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্থায়ী শান্তির পথে সাফল্যের একটি মাইল ফলক। দীর্ঘ কয়েক শতক পরে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাঙালি-পাহাড়ী দলমত নির্বিশেষে শান্তিচুক্তির প্রশস্ত সোপান পেরিয়ে আগামী প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাবে এটাই সবার ঐকান্তিক প্রত্যাশা। আর এতে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে। দলমত নির্বিশেষে তাই এই চুক্তির সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
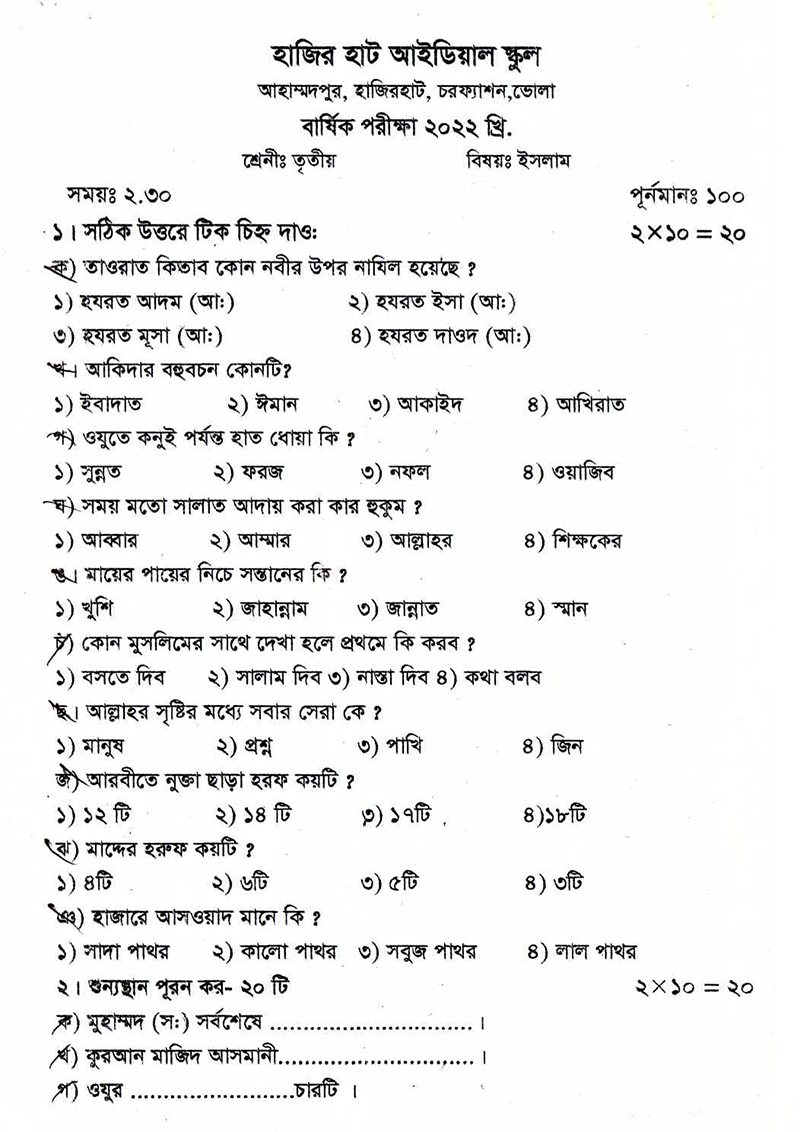










No comments